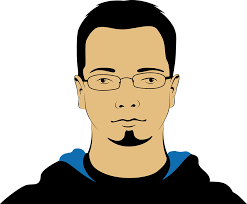

ভূগর্ভস্থ পানি সম্পর্কে আমাদের মাঝে একটি প্রচলিত ভুল ধারণা হচ্ছে—মাটির নিচে বুঝি কোনো নদী বা সমুদ্র বয়ে চলে। বাস্তবে ভূগর্ভস্থ পানি (Groundwater) হলো ভূ-পৃষ্ঠের নিচে থাকা মাটি ও শিলার ছিদ্রযুক্ত স্তরে সঞ্চিত প্রাকৃতিক পানি, যা সাধারণত বৃষ্টিপাত, নদী বা অন্যান্য পৃষ্ঠজল (surface water) থেকে ধীরে ধীরে মাটির গভীরে প্রবেশ করে জমা হয়। এই পানি যে ভূগঠনে সঞ্চিত থাকে তাকে বলা হয় Aquifer, এবং এটি মূলত একটি permeable (পানিপারগম্য) স্তর যা পানি ধারণ ও পরিবহন করতে সক্ষম।এই Groundwater আমাদের চোখে না পড়লেও মানব সভ্যতার জন্য এক নিঃশব্দ জীবনরেখা। বিজ্ঞানীরা একে “সাইলেন্ট রিজার্ভয়ার” (Silent Reservoir) বলেন, কারণ এর অস্তিত্ব দৃশ্যমান নয়, কিন্তু প্রয়োজনীয়তা অপরিসীম। পৃথিবীর মোট মিঠা পানির (freshwater) মধ্যে প্রায় ৩০.১% ভূগর্ভস্থ অবস্থায় থাকে, যেখানে হিমবাহ ও বরফের মধ্যে রয়েছে প্রায় ৬৮.৭% এবং মাত্র ০.৩% পানি নদী, হ্রদ ও জলাশয়ে মজুদ। কিন্তু এই অদৃশ্য ভূগর্ভস্থ পানি পৃথিবীর প্রায় ২.৫ বিলিয়ন মানুষের প্রধান পানীয় জলের উৎস।
বাংলাদেশের প্রেক্ষাপটে এই Groundwater একটি জীবনরক্ষাকারী সম্পদ। দেশের প্রায় ৮৭% মানুষ খাবার পানি এবং প্রায় ৭০% কৃষিকাজের সেচের জন্য সরাসরি এই উৎসের ওপর নির্ভর করে। শহরাঞ্চলে, বিশেষত ঢাকার মতো ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়, পানি সরবরাহকারী সংস্থা ওয়াসা (WASA) তাদের পানির প্রায় ৮৫% ভূগর্ভস্থ উৎস থেকে সংগ্রহ করে। এর বড় কারণ হলো, Surface Water অনেক বেশি দূষিত, বিশেষ করে শিল্পাঞ্চল ও ঘনবসতিপূর্ণ এলাকায়।তবে এই নির্ভরতা ধীরে ধীরে সংকটের দিকে ঠেলে দিচ্ছে। প্রতি বছর ঢাকায় Groundwater Level গড়ে ২–৩ মিটার হারে নিচে নেমে যাচ্ছে। উত্তোলনের হার অত্যন্ত বেশি হওয়ায় Aquifer-এ Recharge হওয়ার যথেষ্ট সময় পাওয়া যাচ্ছে না। ফলে তৈরি হচ্ছে Over-extraction Crisis—যেখানে উত্তোলনের চেয়ে পুনঃভরণ অনেক কম। ঢাকার কিছু এলাকায় এখন পানি তুলতে হচ্ছে প্রায় ৩৫০ মিটার গভীরতা থেকে, যা ভবিষ্যতের জন্য এক ভয়ানক সতর্কবার্তা।একই সঙ্গে, পানি দূষণের (Contamination) ঝুঁকিও বাড়ছে। বাংলাদেশের বহু অঞ্চলে ভূগর্ভস্থ পানিতে পাওয়া যাচ্ছে Arsenic, যা বিশ্বব্যাপী এক গুরুত্বপূর্ণ Public Health Concern. দেশের অন্তত ৬১টি জেলায় আর্সেনিক দূষণের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে। এছাড়াও রয়েছে Iron, Nitrate, Coliform Bacteria ইত্যাদি দূষণ। shallow tube well (অল্প গভীরতার নলকূপ) ব্যবহারে এসব ঝুঁকি বেশি থাকে।Groundwater এর উপস্থিতি এবং গুণমান পুরোপুরি নির্ভর করে Geological Formation এর ওপর। মাটির গঠন, শিলার স্তর এবং Aquifer এর ধরন বুঝে তবেই সিদ্ধান্ত নিতে হয় কোথায় কত গভীরে পৌঁছালে নিরাপদ ও পর্যাপ্ত পানি পাওয়া সম্ভব। দেশের উঁচু এলাকাগুলোতেও একুইফার থাকতে পারে, তবে সেখানে গভীরতা অনেক বেশি এবং ধারকতা (Storage Capacity) কম হতে পারে। কিন্তু যদি সঠিক গভীরতায় পৌঁছানো যায়, তাহলে এসব এলাকাতেও নিরাপদ পানি উত্তোলন সম্ভব।সব মিলিয়ে বাংলাদেশের জন্য Groundwater একদিকে যেমন অত্যন্ত মূল্যবান সম্পদ, তেমনি এটি রক্ষা করা এখন সময়ের দাবিও বটে। এর টেকসই ব্যবস্থাপনা ছাড়া ভবিষ্যতের পানি নিরাপত্তা নিশ্চিত করা সম্ভব নয়।
Intermediate semi-confined aquifer সাধারণত ৩০ থেকে ১৫০ মিটার গভীরতায় পাওয়া যায়। এটি শ্যালো aquifer-এর নিচে অবস্থান করে এবং মাঝখানে একটি সেমি-পারমিয়েবল (semi-permeable) স্তর থাকে, যা আংশিক সুরক্ষা দেয়। এখানকার পানি অনেক অঞ্চলে তুলনামূলকভাবে নিরাপদ, তবে কিছু ক্ষেত্রে সুরক্ষার স্তর পাতলা বা ভাঙা থাকলে দূষণ নিচে নামতে পারে।
Deep confined aquifer, যা সাধারণত ১৫০ মিটার বা তার বেশি গভীরে থাকে, প্রধানত Pleistocene বা Pliocene যুগের rocks এবং sediments, যেমন Dupi Tila formation বা Tipam sandstone দ্বারা গঠিত। এই aquifer-গুলো পুরু clay বা অন্যান্য impermeable স্তর দ্বারা সুরক্ষিত এবং সাধারণত আর্সেনিক ও অন্যান্য দূষণ থেকে মুক্ত থাকে। গভীর aquifer-এর পানি গুণগত দিক থেকে ভালো, তাই শহর ও গ্রামে বিশুদ্ধ পানির প্রধান উৎস হিসেবে এটি ব্যবহৃত হয়। তবে কিছু উপকূলীয় অঞ্চলে গভীর স্তরেও arsenic পাওয়া গেছে, যা hydrogeological জটিলতার ইঙ্গিত দেয়।
এই পুরো aquifer ব্যবস্থার সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত পানি চক্র বা hydrologic cycle। বৃষ্টিপাতের মাধ্যমে পানি মাটির উপর পড়ে infiltration এবং percolation এর মাধ্যমে মাটির নিচে পৌঁছায় এবং aquifer-এ সংরক্ষিত হয়। নদী, খাল, বিল এবং অন্যান্য জলাশয় থেকে seepage এবং recharge প্রক্রিয়ায় aquifer পূর্ণ হয়। আবার বিভিন্ন tube well-এর মাধ্যমে এই পানি উত্তোলন করে ব্যবহৃত হয়। এই প্রাকৃতিক চক্রের মাধ্যমে পানির পুনঃচক্রায়ন হলেও অতিরিক্ত উত্তোলন বা recharge হার কমে গেলে পানির স্তর নেমে যায়, যার প্রভাব পরবর্তীতে সুপেয় পানির সংকটে দেখা দেয়।বাংলাদেশের বার্ষিক ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ প্রায় ২১ কিউবিক কিলোমিটার (২১ বিলিয়ন ঘনমিটার) হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। এই রিচার্জ মূলত বর্ষাকালে বৃষ্টিপাত, নদী প্রবাহ ও প্লাবনের মাধ্যমে ঘটে।ঢাকায় বার্ষিক ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ প্রায় ৬৩৫.৩৫ মিলিয়ন ঘনমিটার, যা বার্ষিক বৃষ্টিপাতের সমান। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে বার্ষিক ভূগর্ভস্থ পানির রিচার্জ প্রায় ৫,১৪৫ মিলিয়ন ঘনমিটার এবং ডিসচার্জ প্রায় ২,৭৭২ মিলিয়ন ঘনমিটার। বিভিন্ন গবেষণায় দেখা গেছে যে, ভূগর্ভস্থ পানির স্তর ক্রমাগত হ্রাস পাচ্ছে, বিশেষ করে উত্তরাঞ্চলে। ২০০১ থেকে ২০২০ সালের মধ্যে ভূগর্ভস্থ পানির প্রবাহের গতি প্রতি বছর ৫,৯০০ থেকে ৭,৩০০ মিটার পর্যন্ত বৃদ্ধি পেয়েছে, যা অতিরিক্ত উত্তোলনের ইঙ্গিত দেয়। সুতরাং, ভূগর্ভস্থ পানির ব্যবহার ও সংরক্ষণের ক্ষেত্রে আমাদের আরও সচেতন হতে হবে। আর্সেনিক ঝুঁকি, অতিরিক্ত উত্তোলন, অবৈজ্ঞানিক নলকূপ স্থাপন এবং জলবায়ু পরিবর্তনের প্রভাবে aquifer গুলো চাপে রয়েছে। সাধারণ জনগণের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি, পানির সঠিক ব্যবহার, বৃষ্টির পানি সংরক্ষণ এবং বৈজ্ঞানিক ভিত্তিতে নলকূপ স্থাপন করলে এই মূল্যবান সম্পদকে ভবিষ্যতের জন্য রক্ষা করা সম্ভব হবে।